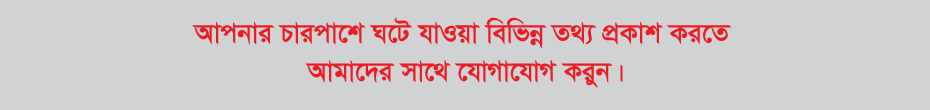মিঠুন রানাঃঢাকার মোহাম্মদপুরের এক আবাসিক এলাকার ১৬ বছর বয়সী আরাফাত রহমান গত তিন দিন ধরে টানা মোবাইল গেম **ফ্রি ফায়ারে** বুঁদ হয়ে আছেন। পড়ালেখা, খাওয়া-দাওয়া, এমনকি পরিবারের সঙ্গে কথোপকথন—সবকিছুই যেন তার জন্য গৌণ হয়ে উঠেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, গেমিং ডিসঅর্ডারকে এখন মানসিক রোগ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশে ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের সহজলভ্যতা এই সমস্যাকে মহামারীর রূপ দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিশোরদের একটি বড় অংশ এখন ভার্চুয়াল জগতের নেশায় বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ মেট্রিক্সের সাম্প্রতিক জরিপে উঠে এসেছে উদ্বেগজনক তথ্য। ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী ৬৫% কিশোর প্রতিদিন গড়ে ৫-৬ ঘণ্টা অনলাইন গেমিংয়ে ব্যয় করে। এর মধ্যে প্রায় ৪০% শিক্ষার্থীর একাডেমিক ফলাফল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ৩০% পরিবারে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে বলে জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে। গেমিং কমিউনিটিতে ভার্চুয়াল বন্ধুত্ব বাড়লেও বাস্তবে একাকিত্ব বাড়ছে বলে মত দিচ্ছেন মনোবিদরা।
এই আসক্তির পেছনে কাজ করছে একাধিক কারণ। প্রথমত, পরীক্ষার চাপ, পারিবারিক প্রত্যাশা বা সামাজিক উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেতে কিশোররা গেমিংকে আশ্রয় হিসেবে বেছে নিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, **পাবজি**, **ফ্রি ফায়ার**-এর মতো গেমগুলোর লুট বক্স, র্যাংকিং সিস্টেম এবং চটকদার স্কিন তাদের মানসিকভাবে আবদ্ধ করে রাখে। তৃতীয়ত, অনেক কিশোর গেমিং ইউটিউবারদের দেখে ভাবছে, এটিও পেশা হতে পারে। তবে মনোবিদ ড. ফারহানা ইসলাম সতর্ক করেছেন, “গেমের রিওয়ার্ড সিস্টেম মস্তিষ্কে ডোপামিনের নেশা সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীতে উদ্বেগ ও হতাশার কারণ হয়।”
স্বাস্থ্যগত প্রভাবও কম নয়। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হওয়া, ঘুমের ব্যাঘাত, স্থূলতা এবং মেরুদণ্ডে ব্যথা—এগুলো এখন সাধারণ সমস্যা। মানসিকভাবে অনেকেই হয়ে পড়ছে আগ্রাসী বা বিচ্ছিন্ন। পড়ালেখায় অমনোযোগিতার পাশাপাশি অনলাইন ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাও বাড়ছে। স্কুলশিক্ষক তাসনিমা আক্তার জানান, “অনেক শিক্ষার্থী ক্লাসের লিংক জয়েন করেই গেম শুরু করে দেয়। এভাবে তারা পুরো জেনারেশনের পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে আছে।”
এই সংকট মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগের তাগিদ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে—সন্তানের সঙ্গে গেমিং বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে এবং স্ক্রিন টাইম সীমিত রাখতে। কিছু স্কুল ই-স্পোর্টস ক্লাব চালু করে গেমিংকে সৃজনশীলতার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে গেম ডিজাইনে বাধ্যতামূলক ব্রেক ফিচার যুক্ত করতে এবং লুট বক্সের মতো ম্যানিপুলেটিভ কৌশল নিষিদ্ধ করতে।
মনোবিজ্ঞানী ড. তানভীর আহমেদের মতে, “গেমিংকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয়, বরং ব্যালান্স শেখাতে হবে। কিশোরদের বাস্তব জীবনে খেলাধুলা, শখ এবং পারিবারিক বন্ধন বাড়ালে তারা ভার্চুয়াল জগতের প্রতি কম নির্ভরশীল হবে।” এ প্রসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, “গেমিং দক্ষতা বাড়াতে পারে, কিন্তু সেটি যেন জীবনের মূল লক্ষ্য না হয়।”
সামগ্রিকভাবে, গেমিং আসক্তি রোধে শুধু নিষেধাজ্ঞা নয়, প্রয়োজন সচেতনতা ও বিকল্প বিনোদনের সুযোগ তৈরি করা। পরিবার, শিক্ষক, নীতিনির্ধারক এবং গেম ডেভেলপারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে এই প্রজন্মকে ভার্চুয়াল ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে। মনে রাখতে হবে, গেমিং জীবনের সমাধান নয়—জীবনটাই যেন শেষ পর্যন্ত গেম না হয়ে যায়!